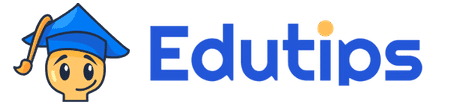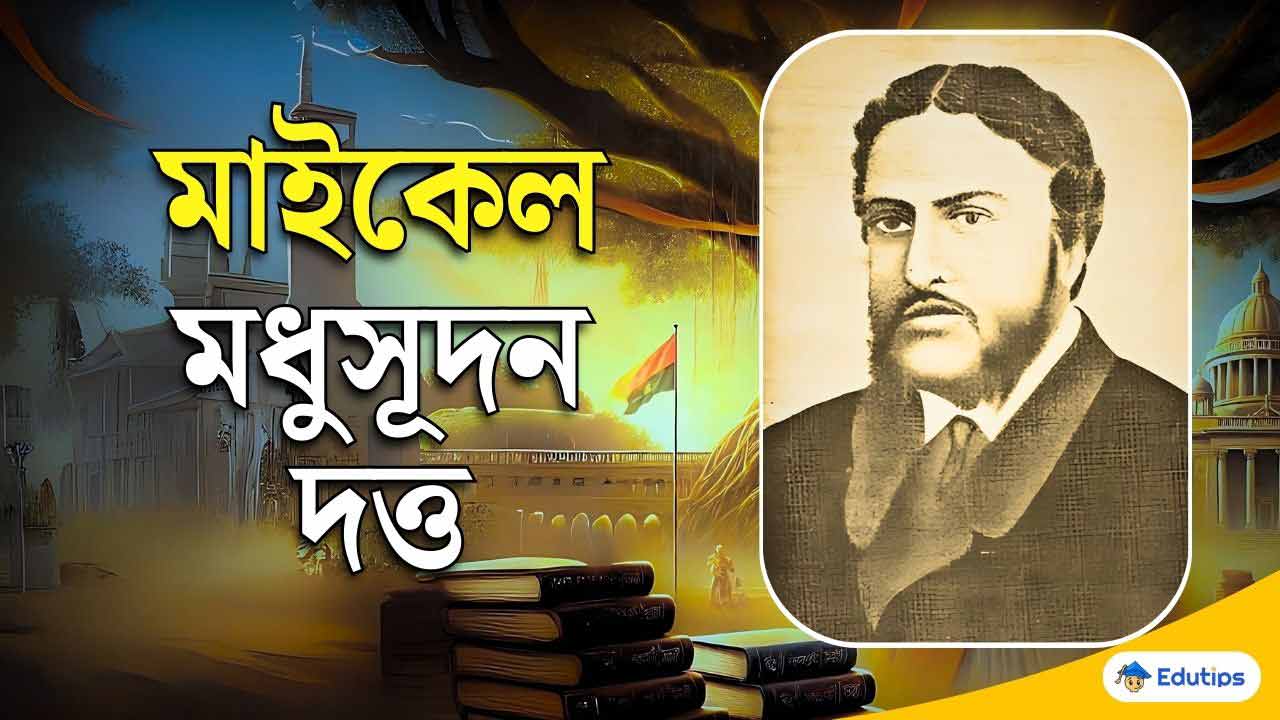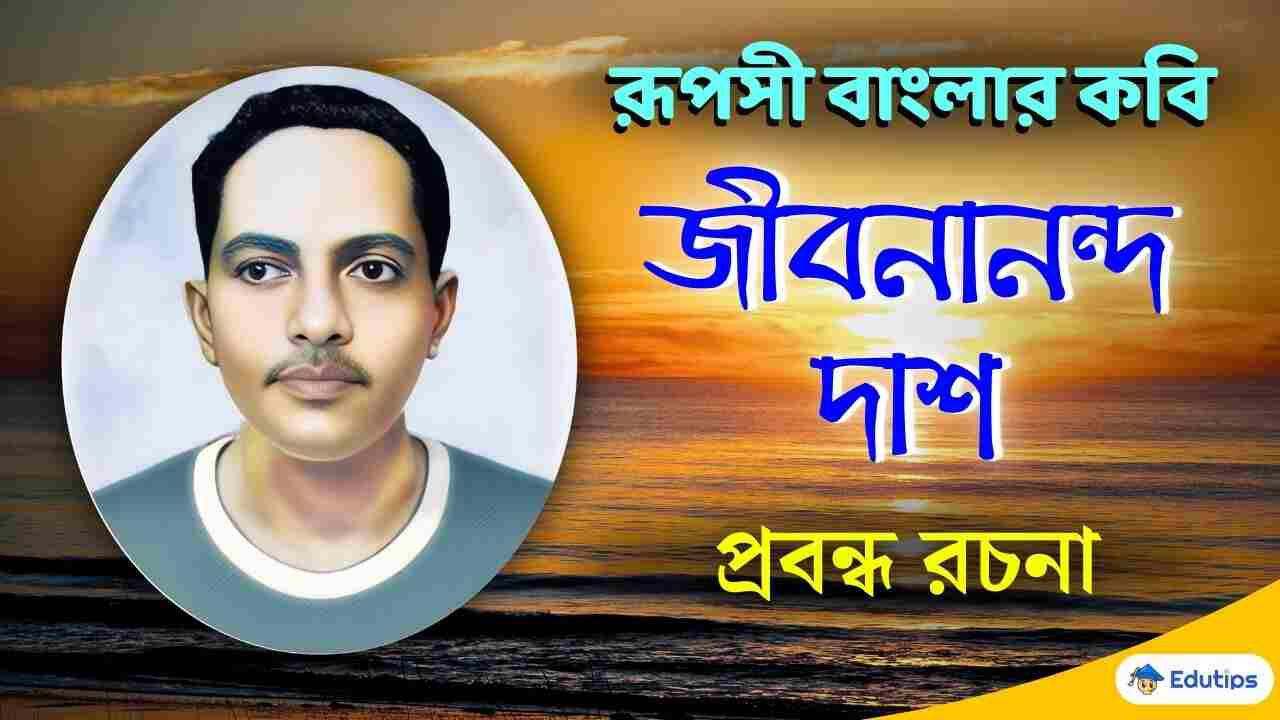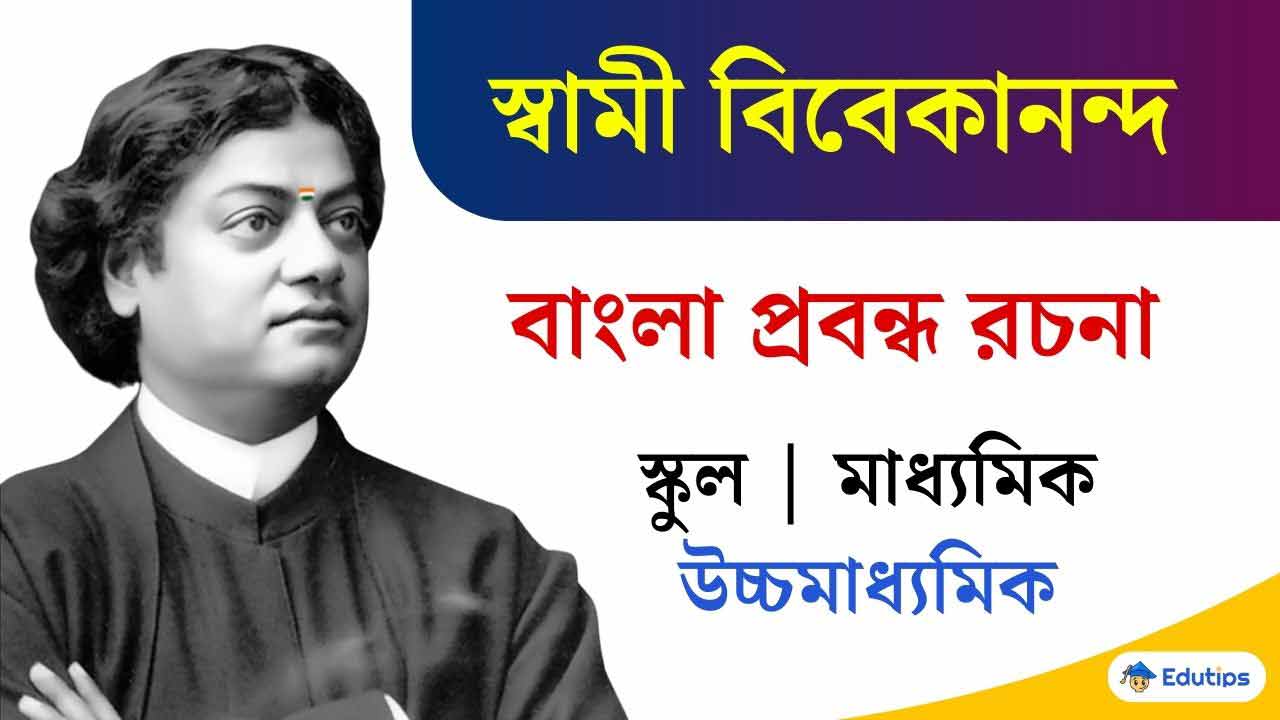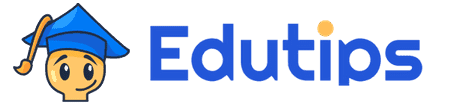🔹 মাইকেল মধুসূদন দত্ত – প্রবন্ধ রচনা 🔹 আজ তোমাদের জন্য নিয়ে এলাম বাংলা সাহিত্যের অমর কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত-এর উপর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ রচনা। উচ্চমাধ্যমিকসহ বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় এটি অত্যন্ত সহায়ক হতে পারে। তাই যারা পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছ, তারা অবশ্যই এটি ভালো করে পড়ে নাও এবং সংগ্রহ করে রাখো।
দ্বিশতবর্ষে মাইকেল মধুসূদন দত্ত
ভূমিকা:
“জীবনে যাহা কিছু বড়ো, বিদ্রোহ তাহার মূল।”
মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাংলা সাহিত্য এক অনন্য নাম, এক চিরবিদ্রোহী প্রতিভা ‘বঙ্গ ভারতীর দামাল পুত্র‘। বাংলা কাব্যধারাকে যিনি ইউরোপীয় রীতি ও আধুনিকতার সংস্পর্শে এনে এক নতুন দিগন্তে নিয়ে গিয়েছিলেন, তিনি আমাদের মধুসূদন। আজ, তাঁর জন্মের দ্বিশতবর্ষে তাঁকে স্মরণ করা শুধু কর্তব্য নয়, এক বিরাট সাহিত্যিক দায়ও বটে।
জন্ম ও বংশপরিচয়:
১৮২৪ সালের ২৫ জানুয়ারি, ব্রিটিশ ভারতের যশোর জেলার সাগরদাঁড়ি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন মধুসূদন দত্ত। তাঁর পিতা ছিলেন রাজনারায়ণ দত্ত, একজন ধনী জমিদার ও আইনজীবী, এবং মাতা ছিলেন জাহ্নবী দেবী। ধনী পরিবারের সন্তান হওয়া সত্ত্বেও মধুসূদনের মন কেবলমাত্র পার্থিব সুখ-সুবিধার প্রতি আকৃষ্ট ছিল না, বরং তাঁর ছিল স্বপ্ন ও উচ্চাশার পাখা মেলা এক উদার চিন্তাধারার মন।
ছাত্রজীবন ও ধর্মান্তর:
মধুসূদনের প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয় মায়ের কাছে। পরবর্তীতে তিনি কলকাতার খিদিরপুরে একটি স্কুলে ভর্তি হন এবং পরে হিন্দু কলেজে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী ও সৃজনশীল ছাত্র, প্রতি বছর বৃত্তি পেতেন। এখানে শিক্ষাগ্রহণ কালে তিনি সহপাঠী হিসেবে ভূদেব মুখোপাধ্যায়, গৌর দাস বসাক, ভোলানাথ চন্দ্র, বন্ধুবিহারী দত্তের মত বন্ধুদের পেয়েছিলেন। যাঁরা পরবর্তীকালে স্ব স্ব ক্ষেত্রে স্বনামধন্য হয়েছিলেন।
১৮৪৩ সালে, উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও পশ্চিমা সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগ তাঁকে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণে প্ররোচিত করে। ফলস্বরূপ, তিনি পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হন এবং অর্থনৈতিক কষ্টের মুখোমুখি হন।
প্রবাস ও কর্মজীবন:
মধুসূদন ভাগ্যের সন্ধানে দক্ষিণ ভারতের মাদ্রাজে (অধুনা চেন্নাই) চলে যান, যেখানে তিনি ইংরেজি পত্রিকা সম্পাদনা করতেন এবং শিক্ষকতা করতেন। এখানেই তিনি ব্রিটিশ বংশোদ্ভূত রেবেকা ম্যাকটিভিসকে বিয়ে করেন। ইংরেজি সাহিত্যে তাঁর অনুরাগ থাকলেও, পরবর্তীতে বাংলা সাহিত্যে তাঁর অবদানই তাঁকে অমর করে রেখেছে।
বাংলা সাহিত্য ও বিদ্রোহী মনন:
মধুসূদনের সাহিত্যজীবনের মোড় ঘুরে যায় যখন তিনি বুঝতে পারেন যে ইংরেজি নয়, বরং মাতৃভাষাতেই তিনি প্রকৃত কাব্যরস প্রকাশ করতে পারবেন। তিনি বাংলা সাহিত্যে নতুন ধারার প্রবর্তন করেন, যেখানে ইউরোপীয় কাব্যরীতি, গদ্যশৈলী ও নাটকের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল ভারতীয় রসায়ন।
কাব্যসৃষ্টি ও মহাকাব্য:
“মেঘনাদবধ কাব্য” তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, যা বাংলা সাহিত্যের প্রথম মহাকাব্য হিসেবে বিবেচিত হয়। এতে রাবণের পুত্র মেঘনাদের মৃত্যুর কাহিনি বর্ণিত হয়েছে, তবে তা প্রচলিত রামায়ণের দৃষ্টিকোণ থেকে নয়, বরং নতুন এক মহাকাব্যিক ভাবধারায়। এ কাব্যের প্রতিটি চরণ যেন বেদনার্ত, অথচ বিদ্রোহের অগ্নিশিখায় প্রজ্জ্বলিত।
তাঁর অন্যান্য সাহিত্যকর্ম:
- ‘শর্মিষ্ঠা’ (নাটক)
- ‘পদ্মাবতী’ (নাটক)
- ‘তিলোত্তমা সম্ভব’ (খণ্ডকাব্য)
- ‘ব্রজাঙ্গনা’ (কাব্য)
- ‘বীরাঙ্গনা’ (পত্রকাব্য)
- ‘চতুর্দশপদী কবিতা’ (বাংলায় সনেট প্রবর্তন)
- ‘একেই কি বলে সভ্যতা’ ও ‘বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ’ (প্রহসন)
সাহিত্য বৈশিষ্ট্য ও মূল্যায়ন:
- বাংলা সাহিত্যে মহাকাব্যের জনক।
- বাংলা কবিতায় গদ্য ভাষার প্রথম প্রয়োগ।
- বাংলা নাটক ও প্রহসনের বিকাশে অগ্রণী ভূমিকা।
- বাংলা সাহিত্যে ইউরোপীয় প্রভাব ও রোমান্টিকতার প্রবক্তা।
- বাংলা সনেট রচনার পথিকৃৎ।
ব্যক্তিগত জীবন ও অর্থসংকট:
মাইকেলের জীবন ছিল চরম নাটকীয়তা ও বিষাদে ভরা। তিনি ফরাসি নারী হেনরিয়েটাকে বিয়ে করেন এবং প্যারিসে অবস্থানকালে চরম অর্থসংকটে পড়েন। বিদ্যাসাগরের সাহায্যে তিনি সংকট থেকে রক্ষা পান। পরে ব্যারিস্টারি পাশ করে কলকাতায় ফিরে আইনজীবী হিসেবে কাজ শুরু করেন, কিন্তু পেশায় সাফল্য পাননি।
মৃত্যু ও উত্তরাধিকার:
১৮৭৩ সালের ২৯ জুন, চরম দারিদ্র্য ও অসুস্থতার মধ্যে মাত্র ৪৯ বছর বয়সে তাঁর জীবনাবসান ঘটে। তাঁর শেষদিনগুলিতে তিনি লিখেছিলেন:
“হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন;…….
মাতৃ-ভাষা-রূপে খনি, পূর্ণ মণিজালে॥”
উপসংহার:
মাইকেল মধুসূদন দত্ত একাধারে বিদ্রোহী, একাধারে শোকের কবি। তাঁর সাহিত্যপ্রতিভা আমাদের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে এবং নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। তাঁর জীবন ছিল সংগ্রামময়, কিন্তু তাঁর সাহিত্য আমাদের চিরকালীন সম্পদ। আজ, তাঁর দ্বিশতবর্ষে, আমরা গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার সঙ্গে এই মহান কবিকে স্মরণ করি।
“নহে নহে, প্রিয় বঙ্গ, ভাবিও না মনে জলদ আশন বসি আছি ভূ-মন্ডলে!”
শতকোটি প্রণাম এই চিরবিদ্রোহী প্রতিভার প্রতি!
আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ ও টেলিগ্রাম Study গ্রুপে যুক্ত হোন -